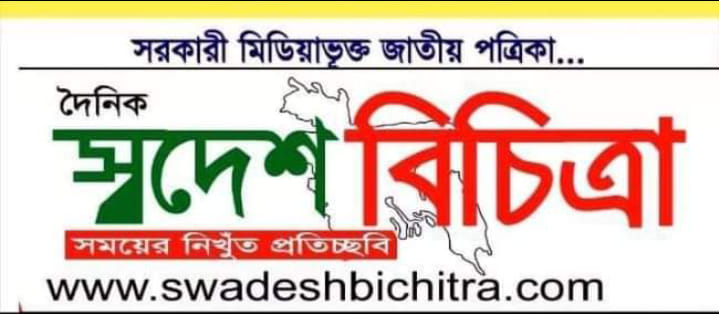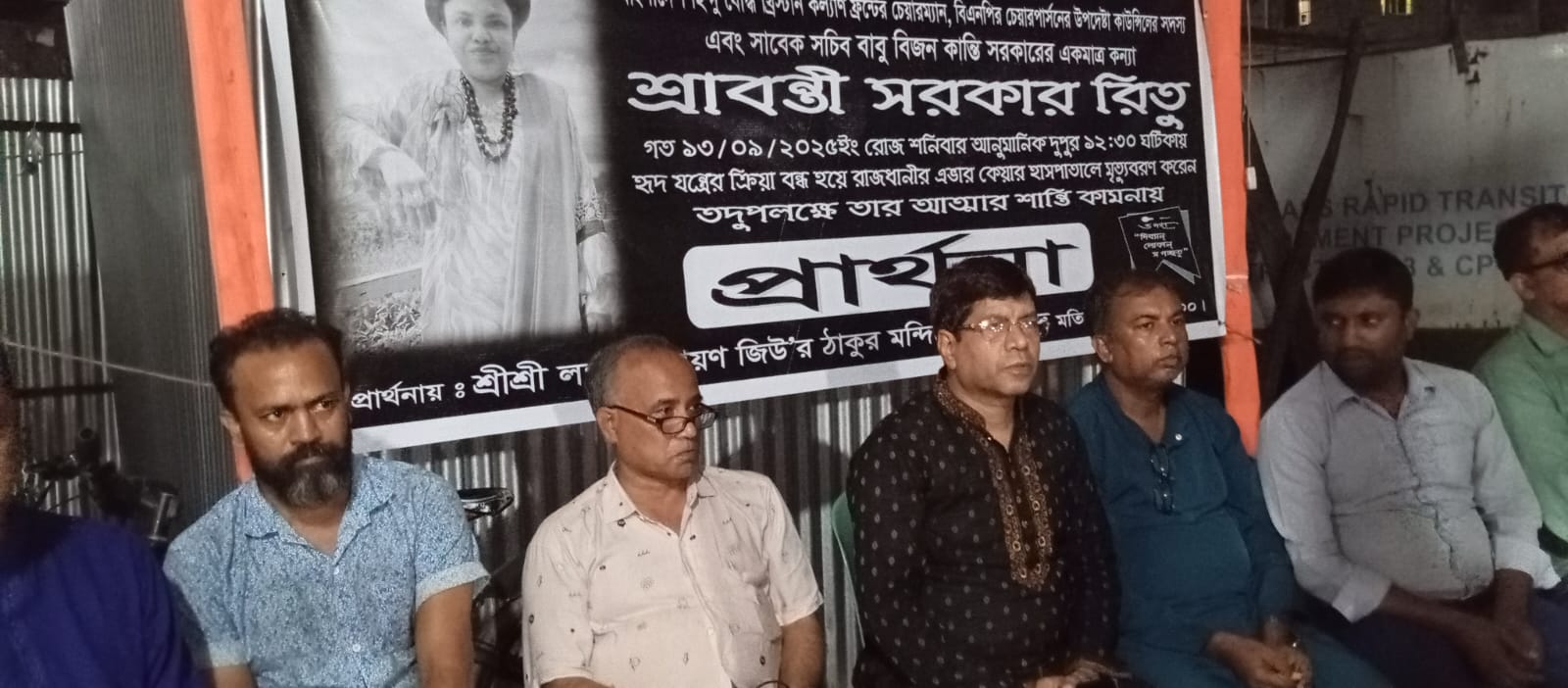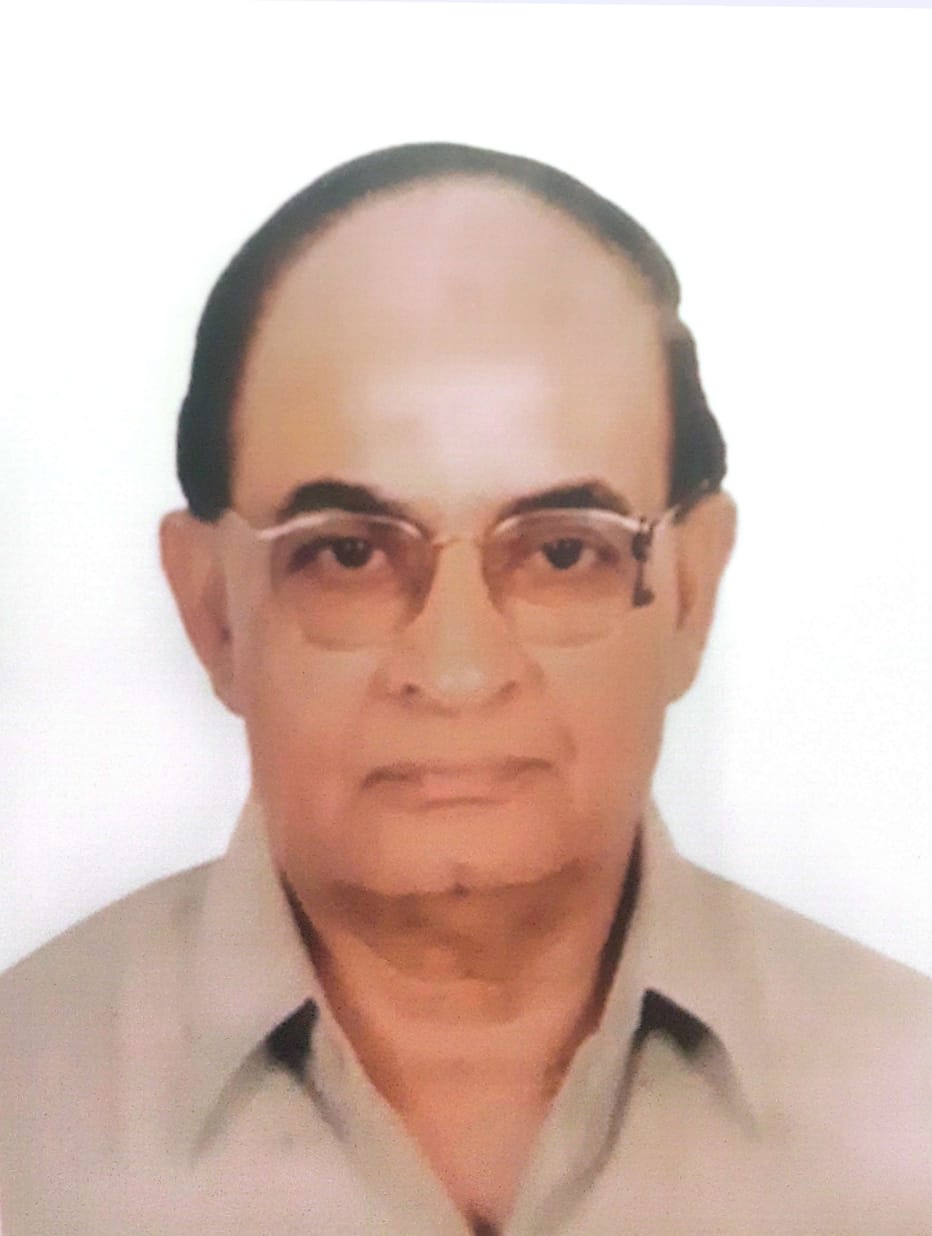বাংলাদেশে ডিজিটাল রূপান্তরের ঢেউ গত এক দশকে নানা খাতে নতুন প্রকল্প এনেছে। উপস্থিতি ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যেই সরকারি দপ্তর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মাঠ প্রশাসনে চালু হয় ডিজিটাল হাজিরা সিস্টেম—আঙুলের ছাপ/মুখমণ্ডল শনাক্তকরণ ও কেন্দ্রীয় সার্ভারে সংযোগিত ডিভাইসের মাধ্যমে কে কখন অফিসে এলেন–গেলেন তার নির্ভুল নথি রাখার কথা ছিল। বাস্তবে, উদ্যোগটি যেখানে নাগরিক সেবায় গতি আনার বদলে কোটি কোটি টাকার অপচয় ও আত্মসাৎ–এর আখড়ায় পরিণত হয়েছে—সেখানে সাংবাদিকদের তথ্যপ্রাপ্তির পথও সংকুচিত হয়েছে। নীতি–নির্ধারণের উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভাষ্য আর মাঠপর্যায়ের জটিল বাস্তবতার এই বৈপরীত্য–ই এখন জনআলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।
উদ্দেশ্য ছিল সংস্থাগুলোর দৈনিক শৃঙ্খলা ও কর্মক্ষমতা মাপা, কিন্তু প্রয়োগে দেখা গেছে—অনেক অফিসে মেশিন স্থাপনের প্রক্রিয়া কাগজে সাঙ্গ হলেও বাস্তবে ডিভাইস কখনও বসেনি, বসলেও কয়েক সপ্তাহ/মাসের মধ্যে অকেজো হয়ে পড়েছে। কোথাও নেটওয়ার্কসংযোগ নেই, কোথাও বিদ্যুৎ–নির্ভরতা ও অনির্ভরযোগ্য ব্যাটারি–ব্যাকআপে সিস্টেম ঘনঘন বন্ধ হয়ে যায়। ডেটা সেন্টারে লগ জমা পড়ার কথা থাকলেও, “সাফল্য প্রতিবেদন”–এ ফাঁপা সংখ্যা দেখিয়ে টেন্ডার–ডেলিভারি ও মাইলস্টোন “সম্পন্ন” দেখানো হয়। যে কোনো প্রযুক্তি–প্রকল্পে যে তিনটি স্তম্ভ—হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার ও প্রক্রিয়া—এখানে তিনটিতেই সমন্বয় ঘাটতি স্থায়ী রূপ পেয়েছে।
মাঝারি ও নিম্নপদস্থ কর্মীদের অভিযোগ—দিনের শুরুতে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে আঙুলের ছাপ দেওয়ার পরও “ম্যাচ ফেলড” দেখায়; শুষ্ক হাত, ধুলা, বা পুরোনো সেন্সরের কারণে বারবার চেক-ইন ব্যর্থ হয়। সার্ভার ডাউন হলে লগ আপলোড হয় না; পরে “ম্যানুয়াল অ্যাডজাস্ট”–এর অজুহাতে কাগজে-কলমে হাজিরা রেট্রো–এন্ট্রি দেয়া হয়। ফলে ডিজিটাল হাজিরা হয়ে উঠেছে এক দ্বৈত ব্যবস্থা—উপরে “ডিজিটাল”, ভেতরে পুরোনো কেরানী–নির্ভর রুটিন। এতে প্রকল্পের মূল প্রতিশ্রুতি—সময়ানুবর্তিতা ও দায়বদ্ধতার স্বয়ংক্রিয়তা—খসে পড়ে।
ক্রয়–প্রক্রিয়ায় অভিযোগ—সীমিত সংখ্যক সরবরাহকারী একধরনের সিন্ডিকেট সুবিধা পেয়েছে। বাজারদরের তুলনায় যন্ত্রপাতির কোট ধরা হয়েছে কয়েকগুণ বেশি, এবং সফটওয়্যার লাইসেন্স/সাপোর্ট–ফি বার্ষিকভাবে ফুলিয়ে–ফাঁপিয়ে বিল তোলা হয়েছে। বহু জায়গায় পুরোনো ডিভাইস ‘রিফারবিশড’ করে “নতুন” হিসেবে সংযোজনের অভিযোগ আছে; অন্যত্র প্রোপ্রাইটারি সফটওয়্যার দিয়ে ভেন্ডর–লক–ইন সৃষ্টি করে ভবিষ্যতের রক্ষণাবেক্ষণকে ব্যবসায়িকভাবে জিম্মি করা হয়েছে। প্রকল্প–রিপোর্টে ডিভাইস–আপটাইম, সক্রিয় ব্যবহারকারী বা মাসিক লগ–ইভেন্টের মতো সূচকের স্বতন্ত্র যাচাই না থাকায়, সংখ্যাগুলো নিরীক্ষাহীন বয়ান হয়ে থেকেছে—যার আড়ালে গিলে ফেলা হয়েছে জনতার করের বিপুল অর্থ।
এই অনিয়মের সূত্র ধরতে গিয়ে সংবাদকর্মীরা বারবার অদৃশ্য দেয়ালে ধাক্কা খান। তথ্য অধিকার আইনের আওতায় আবেদন করেও আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়সীমায় তথ্য মেলে না; “জনস্বার্থে প্রকাশযোগ্য নয়” বা “নিরাপত্তাজনিত গোপনীয়তা”–র অতিরঞ্জিত ব্যাখ্যায় অস্বীকৃতির ভাষ্য হাজির হয়। কারও কারও অ্যাক্রেডিটেশন ঝুলে যায়, মাঠে কাভার করতে গেলে “উর্ধ্বতন অনুমতি”–র গোলকধাঁধায় পাঠানো হয়। ফোন কলে “এখন কথা বলা যাবে না”, “লিখিতভাবে পাঠান”—এমন দীর্ঘসূত্রতা শেষে নতুন ফাইল–নতুন তারিখ—তথ্যপ্রবাহ আটকে দেয়া হয় নিপুণ আমলাতান্ত্রিকতায়। জেলা–উপজেলায় তো আরও জটিল—স্থানীয় শক্তিধরদের অনানুষ্ঠানিক সতর্কতা সাংবাদিকদের আত্মনিয়ন্ত্রণে বাধ্য করে, ফলে অভিযোগ সমর্থনকারী কাগজপত্র প্রকাশ্যে আসে না।
প্রযুক্তি যোগ করে ‘স্বচ্ছতা’ আনার প্রতিশ্রুতি যখন ডেটার অস্বচ্ছতায় আটকে যায়, তখন সেটি দ্বিগুণ ক্ষতি ডেকে আনে। প্রথমত, নাগরিক–সেবার গতি বাড়ে না; দ্বিতীয়ত, সংস্কারের কথা বলে যে রাজনৈতিক–সামাজিক পুঁজি বিনিয়োগ করা হয়, সেটিও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অনেকে বলেন, ডিজিটাল হাজিরার লগ–ডেটা কেন্দ্রীভূত হলেও, অডিটেবল ট্রেইল না থাকলে—কে, কখন, কীভাবে এন্ট্রি সম্পাদনা করেছে—তার কোনো দৃশ্যমান জবাবদিহি থাকে না। ফলে “ডিজিটাল” লেবেলটি ছায়া–স্বচ্ছতা (Shadow Transparency) তৈরি করে—উপরিতলে ফাইল, ভিতরে ফাঁক।
দপ্তরের ভেতরে ক্রস–ডিপেন্ডেন্সি—আইটি সেল, প্রশাসন, অর্থ ও প্রোকিউরমেন্ট—সবাই যখন “অন্য বিভাগের অপেক্ষা” করে, তখন প্রকল্পের দৈনন্দিন সমস্যাও টেকসই ত্রুটি হয়ে ওঠে। ডিভাইস–রিপ্লেসমেন্টের রিকুইজিশন মাসের পর মাস পড়ে থাকে; বাজেট–রিলিজে বিলম্ব; টেন্ডারের আপিল–অভিযোগে প্রক্রিয়া স্থগিত; এদিকে মাঠের ব্যবহারকারীরা অস্থায়ী ম্যানুয়ালে ফিরতে থাকে। সময়ের সঙ্গে এই সাময়িকতা স্থায়ী হয়ে যায়, আর মাসের শেষে রক্ষণাবেক্ষণ বিল ঠিকই পাস হয়। যে-কোনো সংস্কার–এজেন্ডার সবচেয়ে বড় বাধা—এই প্রাতিষ্ঠানিক জড়তা।
ডিজিটাল রূপান্তর নিয়ে তরুণদের উচ্চ প্রত্যাশা ছিল—ডেটা–নির্ভর শাসন, ওপেন ড্যাশবোর্ড, রিয়েল–টাইম মনিটরিং, এবং ‘লগ–চলবে, গাফিলতি বন্ধ’—এই ধারনায় বিশ্বাসী অনেকেই এখন সিস্টেম–থকানিতে আক্রান্ত। বিশ্ববিদ্যালয়–শিক্ষার্থীদের একাংশ সরকারি চাকরির প্রস্তুতিতে যে “ডিজিটাল–গভর্ন্যান্স”–এর গল্প শুনেছেন, মাঠের কেস–স্টাডি তাদের সন্দিগ্ধ করেছে। নাগরিকেরা সেবাকেন্দ্রে গিয়ে দেখছেন—লাইনে দাঁড়ানো বদলেছে, সময়–ব্যয় ও প্রতীক্ষা নয়; অথচ সংবাদ–বিজ্ঞপ্তিতে “সফল ডিজিটালাইজেশন”–এর ভাষা অব্যাহত।
প্রশাসনবিদদের মতে, হাজিরা–সিস্টেম কোনো জাদুর কাঠি নয়; এটি কেবল গভর্ন্যান্স টুলচেইনের একটি নোড। কাজের জায়গা—নীতিমালা–প্রক্রিয়া–ডেটা–মানবসম্পদ—এই চতুর্ভুজে সমন্বয় না হলে যেকোনো প্রযুক্তিই “বাক্স–বন্দি শৃঙ্খলা” হয়ে পড়ে। তাদের ভাষায়, “উপস্থিতি–মনিটরিংকে যদি পারফরম্যান্স–ইভ্যালুয়েশন, পে–রোল, লিভ ম্যানেজমেন্ট ও শাস্তিমূলক বিধিমালার সঙ্গে শক্তভাবে না বাঁধা যায়, তবে ডিজিটাল হাজিরা কেবল চেক–ইন/আউট–রেকর্ডারে রয়ে যাবে—সংস্কারে যাবে না।” তারা আরও বলেন, দেশজ বাস্তবতায় বিকল্প প্রমাণ (যেমন ফিল্ড স্টাফের জিও–ট্যাগড কাজের রিপোর্ট) ও ডিভাইস–অ্যাগনস্টিক অ্যাক্সেস (মোবাইল–কিয়স্ক–কার্ড) না থাকলে, হঠাৎ ডিভাইস–ভেঙে পড়লে ম্যানুয়াল–স্লিপেজ স্বাভাবিক হয়ে যায়।
সরকারি ক্রয়ে “অসুস্থ প্রতিযোগিতা” দেখলে বিশেষজ্ঞরা সাধারণত তিনটি সংকেত খোঁজেন—(১) একই ভেন্ডরের ধারাবাহিক আধিপত্য, (২) যুক্তির বাইরে মূল্যবৃদ্ধি, (৩) রক্ষণাবেক্ষণ–চুক্তিতে অস্পষ্টতা। তাদের ব্যাখ্যায়, “হার্ডওয়্যারে একরকম কস্ট–ক্লাস্টার, সফটওয়্যারে প্রোপ্রাইটারি মোড়ক, মেইনটেন্যান্সে কাল্পনিক ‘কনসালটেন্সি’—এই ত্রিস্তরেই ফুলে–ফাঁপা বিলের জন্ম হয়।” নিরীক্ষা–দৃষ্টিতে সবচেয়ে দুর্বল কড়ি—স্বাধীন যাচাইয়ের অভাব; সরবরাহকারী যা বলেছে, রিপোর্টে তাই—তৃতীয় পক্ষের ফিল্ড–ভেরিফিকেশন বিরল। ফল—সংখ্যা আছে, নিশ্চয়তা নেই।
প্রযুক্তি–বিশেষজ্ঞদের মতে, হাজিরা–সিস্টেমকে সাইবার–রেজিলিয়েন্স ছাড়া ভাবা যায় না। ডেটা–অখণ্ডতা (Integrity) রক্ষায় চাই—ইম্যুটেবল লগিং, রোল–বেসড এক্সেস, টাইম–স্ট্যাম্পড এডিট–ট্রেইল, এবং অ্যানোমালি–ডিটেকশন (যেমন একই ব্যক্তি একই সময়ে দুই জায়গায় হাজিরা দিলেন কিনা)। তারা সতর্ক করেন: “ডিভাইস বসিয়ে ছবি তোলা উন্নয়ন নয়; উন্নয়ন তখনই, যখন লগ–ডেটা দিয়ে অপারেশনাল সিদ্ধান্ত বদলে যায়।” যদি মনিটরিং বোর্ডে আপটাইম, ফেলিওর–কাউন্ট, মিসিং–সিঙ্ক, রিজেক্টেড–ম্যাচ–এর মতো সূচক দৃশ্যমান না হয়, তবে আইটি বিভাগও অন্ধকার ঘরে টর্চহীন।
আরটিআই–আইন বিশেষজ্ঞরা মনে করিয়ে দেন—জনস্বার্থে ব্যবহূত প্রতিটি টাকার দলিল নাগরিকের সম্পদ। কোনো প্রকল্পের খুঁটিনাটি—ডিভাইস ইউনিট–কস্ট, বার্ষিক সাপোর্ট–ফি, ডেলিভারি–মাইলস্টোন—এসব তথ্য “প্রকাশযোগ্য নয়” বলা আইনগতভাবে অসাংগতিক। তাদের ভাষা, “গোপনীয়তার ব্যাখ্যা যেখানে ন্যূনতম, সেখানে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা সর্বোচ্চ—এই নীতি যে দেশ মেনে চলেছে, সেখানেই ডিজিটালাইজেশন সত্যিকারের সাফল্য।” সাংবাদিকতা–আইনের পর্যবেক্ষকরা যোগ করেন—মাঠে রিপোর্টিংয়ের সময় হয়রানি/অ্যাক্রেডিটেশন স্থগিত–জাতীয় পদক্ষেপ চilling effect তৈরি করে; ফলে potential whistleblowers–রাও নীরবতা বেছে নেন, যা সিস্টেমিক দায়মুক্তি টেনে আনে।
এইচআর–বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য—হাজিরা আচরণ–পরিবর্তনের একটি ‘নাজ’ (nudge) মাত্র। কর্মঘণ্টা ঠিক, কিন্তু কাজের আউটপুট অস্পষ্ট—তাহলে কর্মী কেবল ডিভাইস–টাচ করে নিজস্ব ‘রুটিন’ চালিয়ে যাবেন। তাদের মতে, “ডিজিটাল নাজ + জব–ডিজাইন + ফিডব্যাক”—এই ত্রয়ী না থাকলে, হাজিরা কেবল বা্যুরোক্র্যাটিক শেল—ভেতরে দাপ্তরিক সংস্কৃতি আগের মতোই। ফলে ব্যবস্থাপনার কাছে হাজিরা–লগ “ডিসিপ্লিন মেট্রিক”, জনতার কাছে তা “কাগজের শাসন”।
ম্যাক্রো–অর্থনীতির ভাষায়—প্রযুক্তি–প্রকল্পে ক্যাপেক্স (যন্ত্র ক্রয়) আর অপেক্স (রক্ষণাবেক্ষণ)–এর অনুপাত, পারফরম্যান্স–ইলাস্টিসিটি (বিলিয়ন টাকা খরচে নাগরিক–সেবায় কত মিনিট/কত ধাপ সাশ্রয়), ও অবসোলেসেন্স রিস্ক (ডিভাইস পুরোনো হয়ে গেলে রিপ্লেস–কস্ট)–—এই সূচকগুলো যদি ভুল–ফোকাসে থাকে, তবে ডেড–ওয়েট লস তৈরি হয়। অর্থনীতিবিদদের সারকথা, “ডেটা–ড্রিভেন গভর্ন্যান্সে বিনিয়োগ করতে গিয়ে যদি ডেটাই অবিশ্বাস্য হয়, তবে সেটি করদাতার অর্থে স্টেরাইল ব্যয়—দেখতে ঝকঝকে, ফল শূন্য।”
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) সাবেক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ বলেন,
“প্রযুক্তি ব্যবহারের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। কিন্তু প্রযুক্তির আড়ালে দুর্নীতি চললে এর প্রভাব আরও ভয়াবহ হয়। জনগণের চোখে সরকারের ভাবমূর্তিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।”
অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন,
“ডিজিটালাইজেশনের নামে প্রকল্প ব্যয় নিয়ন্ত্রণহীন হলে জনগণের করের টাকা অপচয় হয়। এর ফলে সরকারি সেবার মান উন্নত হওয়ার বদলে বরং জনগণের ভোগান্তি বাড়ে।”
সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন)-এর সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার বলেন,
“ডিজিটাল হাজিরা প্রকল্পে সঠিক পর্যবেক্ষণ ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা ছিল না। তাই দুর্নীতির সুযোগ তৈরি হয়েছে। যদি জনগণ ও গণমাধ্যমের অংশগ্রহণ থাকত, তবে এত ব্যাপক অনিয়ম সম্ভব হতো না।”
২০০৯ সালের তথ্য অধিকার আইন নাগরিকদের রাষ্ট্রীয় তথ্য চাওয়ার বৈধ পথ খুলে দিয়েছে—সুনির্দিষ্ট ফর্ম, নির্দিষ্ট সময়সীমা, অস্বীকৃতির সুনির্দিষ্ট যুক্তি। কিন্তু অনুশীলনে দেখা যায়—দপ্তরগুলো প্রায়ই অধিকতর অনুমোদন, কমিটি–রিভিউ বা নিরাপত্তা ব্যাখ্যা দিয়ে বিলম্ব ঘটায়। তথ্য কমিশনে আপিল–অভিযোগের সংখ্যা বলছে—খোলা–তথ্য সংস্কৃতি এখনও ব্যতিক্রম, নিয়ম নয়। অন্যদিকে সরকারি ক্রয়নীতি বই–পুস্তকে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা–র কথা বললেও, বাস্তবে প্রি–বিড মিটিং, টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন–এর নাজুক বয়ান, আর যোগ্যতার কৃত্রিম বাধা—এসব মিলিয়ে এন্ট্রি–বারিয়ার তৈরি হয়, যা সিন্ডিকেট–সুবিধা পাকা করে।
এই প্রকল্পের প্রথম ভুক্তভোগী—সাধারণ মানুষ। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সিরিয়াল সিস্টেম ঠিকমতো চলে না, ভূমি অফিসে সেবার সময়সূচি কাগজে আছে কিন্তু বাস্তবে দরজার সামনে ভিড়, বিদ্যালয়ে শিক্ষক–হাজিরার লগ পূর্ণ—কিন্তু ক্লাসে প্রক্সি বাস্তবতা। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের ডিজিটাল ব্র্যান্ডিং–এ আঁচ লাগে; বাহ্যিকভাবে “স্মার্ট” ভঙ্গি, ভেতরে “ম্যানুয়াল–ওয়ার্ক–অ্যারাউন্ড”—এই দ্বিধাবিভাজন জনগণের মনোজগতে বিশ্বাসের ক্ষয় ঘটায়। তৃতীয়ত, মন্ত্রণালয়–পর্যায়ে রাজনৈতিক মূলধন—‘ডেলিভারি’–র গল্প—যখন মাঠে অভিজ্ঞতাগতভাবে সত্য হয়ে উঠতে পারে না, তখন নীতিনির্ধারণের সামাজিক লাইসেন্স সংকুচিত হয়। সবশেষে, আর্থিক ক্ষতি—যন্ত্রপাতি/সাপোর্টে ডুবে থাকা টাকার সুযোগ–মূল্য; যে অর্থ শিক্ষা–স্বাস্থ্য–পানি–পয়ঃনিষ্কাশনে গেলে মোট সামাজিক উৎপাদন বাড়াতে পারত, তা আটকা পড়ে অকার্যকারিতার কৃষ্ণগহ্বরে।
ডিজিটাল হাজিরা—ধারণায় সরল, প্রয়োগে জটিল। এটি এমন এক “ডিজিটাল আয়না”—যা শাসনের অঙ্গসৌষ্ঠব দেখানোর কথা; কিন্তু আয়নার কাচ যদি ধুলো–কুয়াশায় ঢেকে থাকে—হার্ডওয়্যার নষ্ট, সফটওয়্যার অস্পষ্ট, ডেটা অনি®র্ভুল—তবে প্রতিচ্ছবি শুধু বিকৃত হয়। এই বিকৃতি নাগরিক–অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে—সারিতে দাঁড়ানো সময়, কাউন্টারের সামনে অনিশ্চয়তা, আর সংবাদ প্রতিবেদনে বারবার ফিরে আসা অপ্রাপ্য নথি। প্রযুক্তি–লেবেল যতই আধুনিক হোক, ভেতরে যদি জবাবদিহি–শূন্য সংগঠন কাজ করে, তবে ডিজিটাল হাজিরা কেবল কার্ড–ট্যাপের শব্দ—শাসনের সুর নয়। আর যখন সাংবাদিকদের প্রশ্নের সামনে দরজা বন্ধ হয়ে যায়, তখন জন–আস্থার সেই সুর নিঃশব্দ হয় আরও—শোনা যায় শুধু ফাইল উল্টানোর মৃদু আওয়াজ।