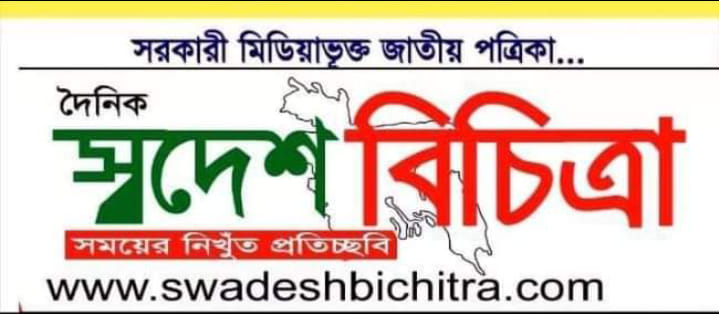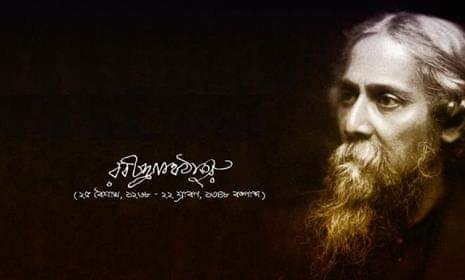রবীন্দ্রনাথ মানবিক মরমি মানুষ। চিরায়ত বিশুদ্ধ গীতিময়তায় বিভোরিত করেছেন বিশ্বসাহিত্যকে। পরম পূর্ণতায়, কাব্যময়তায়, সৃষ্টিশীলতায় তার কবিতা সারা বিশ্বে সমাদৃত হয়েছে। ইংরেজি গীতাঞ্জলি পড়ে মুগ্ধ ইয়েটস ঘোষণা করেছিলেন- রবীন্দ্রনাথ সবার চেয়ে মহত্তর কবি। পাউন্ডের মনে হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি বইয়ের সঙ্গে একমাত্র দান্তের পারাদিসোর তুলনা হতে পারে। কবি স্যাঁ জন পার্স গীতাঞ্জলিতে শুনেছেন বিশ্বহৃদয়ের এক নবীন সুর। আর গীতাঞ্জলি ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করতে গিয়ে আন্দ্রে জিঁদের মনে হয়েছিল, এমন গভীর এবং সুন্দর মৃত্যুর স্তব তিনি আর কোনো সাহিত্যে শোনেননি।
রবীন্দ্রনাথ বহুমুখী প্রভিতার অধিকারী ছিলেন। তার বিশ্বাতীত বোধ ও মনীষা মূলত মানবিকতাকেই নানাভাবে স্পর্শ করেছে। কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, নাটক, নৃত্যকলা, শিশুতোষ ও ছড়া সাহিত্যে সেই মানবিকতার প্রকাশ ঘটেছে। তিনি মানবিক ও মরমি সাধনায় নিজেকে ঋষিতুল্য করে তুলেছেন। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আর মানুষের সঙ্গে মানুষীর বহু বৈচিত্র্য সম্পর্ক উদঘাটন করেছেন তার শিল্প সৃষ্টিতে। শেক্সপিয়র ও ডিকেন্সের মতো রবীন্দ্রনাথ মানুষের চরিত্রগত অন্তহীন বহুধা ও মানবিক দিকের সন্ধানী ছিলেন বহুলাংশে। রামমোহনের মতো রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন পূর্ব ও পশ্চিমকে মেলাতে। ভারতবর্ষকে তার পরস্পরশ্রেয়ী অচলায়তনী জড়তা থেকে উদ্ধার করে বিকাশশীল আধুনিকতায় উদ্বুদ্ধ করতে। রাষ্ট্র সমাজের সম্পর্ক, শক্তির বিকেন্দ্রীয়ান, সহযোগিতাভিত্তিক আর্থ সংগঠন, নর-নারীর সাম্য, জন্মনিয়ন্ত্রণ, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার, মানুষের বিকাশকে সুসাধ্য করার জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও প্রয়োগ, সুপরিকল্পিত শিক্ষার ভেতর দিয়ে ব্যক্তির এবং সমাজের কল্যাণমুখী রূপান্তরসহ নানা বিষয়ে মানুষের মঙ্গলের প্রতি সচেতন ছিলেন।
রবীন্দ্রনাথ নিজে নিজেকে বহু রবীন্দ্রনাথে বিভক্ত করেছেন এবং বলেছেন তিনি হচ্ছেন বহু রবীন্দ্রনাথের মালা। রবীন্দ্র সাহিত্যে, কাব্যে, গল্প-উপন্যাসে মানবিক সম্পর্ক হচ্ছে প্রধান বিষয়। মানব সম্পর্কের দ্বন্দ্বমূলক, প্রতিযোগিতামূলক ও ভক্তিমূলক দিকগুলো বিশেষভাবে ফুটে ওঠে। মূলত রবীন্দ্রনাথ সাধনা করেছেন মানব সম্পর্কের স্বরূপ উদঘাটনের মাধ্যমে উন্নয়ন সাধনের জন্য। চলমান ও সমগ্রবাদী জীবনদর্শন রবীন্দ্র সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্যের উৎস। তার মূলে রয়েছে মানুষের সমগ্র জীবনের অনিঃশেষ ধারণা, রেনেসাঁসের উপলব্ধি ও অঙ্গীকার। তিনি মানুষকে স্থাপন করেন সবকিছুর কেন্দ্রস্থলে। সৌন্দর্যানুভূতি, মর্তপ্রেম ও ধর্মবিশ্বাস হচ্ছে মানবমুখী। জীবন বিমূর্তায়নের শিল্পক্ষেত্র কবিতায় কেবল ব্যক্তিসত্তার প্রকাশেই তিনি তৃপ্ত ছিলেন না। হৃদয়াশক্তি, সৃজনশীলতা ও কল্পনাশক্তির সমন্বয়ে তিনি ব্যক্তির মধ্যে সামগ্রিক অস্তিত্বের ধ্বনি-প্রতিধ্বনিকে সন্ধান করেছেন। মানব জীবনের বহুমাত্রিক রূপ ও স্বরূপের অন্বেষণই তার কবিতার চিরকালের বিষয়বস্তু।
‘ইচ্ছে করে মনে মনে
স্বজাতি হইয়া থাকি সর্বলোকে সনে
দেশে দেশান্তরে’
কবির মর্তপ্রীতি ও বিশ্বপ্রকৃতির অনুধ্যানের মধ্যেও কবির মানবায়নের আকাঙ্ক্ষা সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। মূলত তার কাব্যে প্রকৃতির প্রাণময় সত্তা অনুভব শিল্পস্বভাবের আদি লক্ষণ। নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলি কবিতাগ্রন্থে তার মানবিক ধারণা বিশ্বাত্মাবোধে উন্নীত হয়েছে। সীমা অসীমের মিলন সাধনায় কবি মানুষের যে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন, সেখানে অসীম ঈশ্বর মানুষের মধ্যেই আশ্রয় গ্রহণ করে। কবির ঈশ্বর মানুষের মধ্যেই আশ্রয় গ্রহণ করে। কবির ঈশ্বরভাবনায় পূর্ণাঙ্গ মানবিক মুক্তি লাভ করেছে। মানবপ্রেম তার কাব্য-সাহিত্য চর্চার প্রধান অনুষঙ্গ। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে চিরন্তন মানসিব দ্বন্দ্ব-মধুর সম্পর্ক তার ক্রমাগ্রসরমান উন্নয়ন প্রত্যাশা এবং গভীরভাবে তার সঙ্গে আত্মসম্পৃক্তি কামনা রবীন্দ্র সাহিত্যের মূল উপজীব্য। সমাজ, স্বদেশ আর মানুষই তার কাব্যের কর্ষণক্ষেত্র। মানুষকে দেখেছেন তিনি বহুবিধ সম্পর্কের ভেতর দিয়ে। সামাজিক, ধূর্ততা এবং বৈষয়িক ধর্মবোধের উভয় সংকট সমাধানে তিনি রীতিনীতির প্রতি আস্থাশীল ছিলেন। ১৮৬১ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের জীবনকাল। উপমহাদেশে ঔপনিবেশিক যুগের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় তিনি অবলোকন করেন। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কাঠামোর ভেতর ইংরেজের জীবন ও শাসিত গ্রামীণ কৃষকের জীবনকে অবলোকন করেছেন তার নানা বিষয়ে। মূলত লেখক পাঠক মানব সম্পর্কে ধ্রুপদ ও আপতিক উৎস স্বরূপে চিহ্নিত করা যায়। তার শাশ্বত মূল্যবোধগুলোকে উদঘাটন করে পরিচর্যার মাধ্যমে সমাজ উন্নয়নের জন্য একান্ত অপরিহার্য। হৃদয়াবেগের সঙ্গে কল্পনাশক্তি, কল্পনাশক্তির সঙ্গে মননশীল কৌতূহল কবির বিমূর্ত শিল্পক্ষেত্রকেও মানব জীবনের সংঘাত ও সংগ্রাম ঘিরে আছে। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস সাহিত্যের বিষয় মানব হৃদয় এবং চরিত্র। তার মতে, মানবিক সম্পর্কের বহুমুখী উৎসারণের শব্দরূপই হচ্ছে সাহিত্য।
তিনি মনে করেন, লেখকের নিজরে অন্তরে একটি প্রকৃতি আছে অভিজ্ঞতার সূত্রে, প্রীতি সূত্রে এবং নিগূঢ় ক্ষমতাবলে উভয়ের সম্মিলন হয়। তার কাব্যে হৃদয়ঘেরা মানবিক আবেগের শব্দরূপ জীবনাভিজ্ঞতা ও শিল্পাভিজ্ঞতায় রূপান্তরের ক্রমধারায় কবির সঙ্গে শিল্পীর সম্মিলন ঘটেছে বহুলাংশে। তিনি মনে করেন, সাহিত্যের সেই রূপ সৃজনধর্মী। দর্শন, বিজ্ঞান, প্রকৃতি নির্মাণধর্মী সৃষ্টির মতো সাহিত্যই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। সাহিত্য অর্থেই থাকিবার ভাব, মানুষের সহিত থাকিবার ভাব, মানবকে স্পর্শ করা, মানবকে অনুভব করা।
‘মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবার চাই’
রবীন্দ্রনাথের জীবনাচার ও জীবনাভিজ্ঞতাকে কোনো প্রতিষ্ঠান বাঁধতে পারেনি। মূলত তিনি বাঙালির সাংস্কৃতিক পরিম-লের আদি প্রতিষ্ঠান। তিনি সারা জীবনই ছিলেন আশাবাদী। মানুষের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস ছিল যা তার বিভিন্ন রচনায় প্রতিফলিত। তিনি সত্য সুন্দর ও মানবিক কল্যাণের সাধক। একাধারে কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, গদ্যকার, ছড়াকার, নাট্যকার। যিনি সারা জীবনই নিজের কাছে হাজারো প্রশ্ন করে কোনো স্বার্থ খুঁজে পাননি। অজস্র অমীমাংসিত জিজ্ঞাসার নিরুত্তর ছবি হয়ে প্রতিচ্ছবির অবয়ব খুঁজেছেন। নিজের আয়নায় নিজের স্বরূপ দেখতে গিয়ে মানুষের প্রতি ছড়িয়ে দিয়েছেন অসীম প্রেম। মানুষের অন্তিম সম্ভাবনাকে ঊধর্ে্ব তুলে ধরেছেন সৃষ্টিশীলতায়_
‘সীমার মাঝে অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।’
রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সুদূরপিয়াসী। বিশ্বপথিক ক্রমে হয়ে উঠেছেন বিশ্বনাগরিক। তিনি ১২বার বিশ্ব ভ্রমণ করেন। অস্ট্রেলিয়া ছাড়া পৃথিবীর সব দেশ ভ্রমণ করেছিলেন। প্রকৃতি ও নিসর্গের সৌন্দর্যের প্রভাবই তাকে চিত্রশিল্পী হওয়ার পেছনে নিয়ামক ভূমিকা রেখেছে। তার সৃষ্টি চিরায়ত ও বিস্ময়। তার ভালোবাসার ধর্ম এ পৃথিবী ও মানুষ। শক্তির রূঢ় উন্মত্ততা ও মানবতার চরম অবমাননায় তিনি উদ্বিগ্ন ও পীড়িত হয়েছেন_ কবিতায় সফলভাবে প্রতিফলন ঘটেছে। মানবিকতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাকে তিনি চিন্তায় ও সৃষ্টিতে সচল রেখেছেন। মানব মৈত্রীর বিশুদ্ধ পরিচয়ে বিশ্ব মানুষকে মুক্তির মন্ত্রে উজ্জীবিত করেছেন। সত্য ও জগতের মহিমাধ্যানে একান্ত মনে নিবিষ্ট ছিলেন। বিশ্বজোড়া মানব পীড়নের মহামারী থেকে মানবাত্মার অপমান ভুলে মুক্তির গান গেয়েছেন_
‘শুভ কর্মপথে ধর নির্ভয় গান
সব দুর্বল সংশয় হোক অবসান।’
রবীন্দ্রনাথের কাছে সংস্কৃতিবান ব্যক্তি হচ্ছে সক্রিয়, প্রকাশ উন্মুখ ও অনুভূতির মানুষ। তিনি ভোগের উপকরণের সঙ্গে যুক্ত করেছেন ব্যবসা-বাণিজ্য, কল কারখানা বিস্তারকে। রক্ষণশীল সংস্কৃতির প্রাতিষ্ঠানিক এবং আর্থিক ক্ষমতা ও সাধারণ মানুষের সংস্কৃতি বিষয়ে উদাসীনতার সম্মুখীন হয়ে রবীন্দ্রনাথ সর্বজনীন শিক্ষার দিকে ঝুঁকেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন শিক্ষাই পারে অর্থ ও যন্ত্রের পাশব ক্ষমতা এবং শ্রমজীবী মানুষকে অমানবিক দূষণ থেকে মুক্তি দিতে। সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে চলতে গিয়ে একা হয়ে পড়লেও তিনি তা থেকে কখনো সরে যাননি।
‘মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক
আমি তোমাদেরই লোক’
প্রকৃত অর্থে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এক মানবতাবাদী লেখক। তার সব চিন্তা ও কর্মের কেন্দ্রস্থলের প্রাণশক্তি ছিল মানবকল্যাণ দর্শন। বিশ্বভারতী নামের মধ্যে তার বিশ্বায়নের ধারণা পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বায়ন চেতনা ও বিশ্ব মানবতাবাদ একই অর্থবোধক, অভিন্ন সত্তার অধিকারী। তার মতে, ধর্ম আসলে একটাই_ তা হচ্ছে মানুষের ধর্ম। সারা জীবনই তিনি মানবধর্মের প্রতিরূপ সত্তার লালন করেছেন।
‘জয় জয় জয় রে মানব অভ্যুদয়
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।’
কবিজীবনের বাইরে রবীন্দ্রনাথ সমবায় আন্দোলনেও যুক্ত ছিলেন। আধুনিক চাষাবাদের জন্য ট্রাক্টর ভারতে নিয়ে আসেন। অধিক ফসল ও খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়ে ভেবেছেন। ব্যক্তিজীবনে মন্ত্রসাধকে নিজকে পরিণত করেছেন। ভারত, বাংলাদেশ, নেপালের জাতীয় সঙ্গীত তার রচিত। তিনি চেয়েছেন প্রত্যেক জাতি তার নিজস্ব জাতিগত পরিচয়ে সমৃদ্ধ হবে। সময়-সমাজ-রাষ্ট্র ব্যবস্থার ঊধর্ে্ব তিনি জাতি থেকে আন্তর্জাতিকতায় নিজেকে নিবেদন করেন। তার অমর কবিতা, গান ও গদ্যে শুধু মানুষের যাবতীয় গুণের আন্ত-নিরীক্ষণে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা, নতুনের স্বপ্ন, বিশ্বমানবতায় একাত্ম হওয়ার মন্ত্র দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি, নাটক অভিনয়, নৃত্যকলাসহ বহু বিষয় রেখে গেছেন পৃথিবীর জন্য। তার চেয়ে অধিক মানবতা কী হতে পারে। যিনি সারা জীবনই আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে, সত্য সুন্দরে নিজেকে একীভূত করেছেন। চিরপ্রেমিক গুরুকবি হিসেবে বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যে পরিচিত করেছেন। তার নোবেলপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বসাহিত্যমোদীদের রবীন্দ্রনাথ পাঠে ও বাংলা কবিতা জানার সুযোগ সৃষ্টি হয়। পরম মানবতা ও অধ্যাত্মবোধ তার গানে প্রতিফলিত হয়। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রকৃতির আলো-বাতাস অনুভব করেছেন। বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী-সম্প্রদায়ের জীবনযাপন, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বিষাদের সঙ্গে মিশে গভীরভাবে অবলোকন করেছেন। বিশ্ববীক্ষায় তার জানার পরিসীমা বিস্তৃত করে তিনি হয়ে ওঠেন বিশ্বমানবিক। প্রেম ও মানবতা তার সমগ্র কাব্যকলার মূল সুর। আত্মপ্রেম থেকে অধ্যাত্মপ্রেম, স্বদেশপ্রেম থেকে বিশ্বপ্রেমে তিনি চিন্তাকে নিয়ে গেছেন প্রার্থনা ও পূজায়। তার নতজানু মানবিক সঙ্গীত তাকে দিয়েছে আন্তর্জাতিকতা। করেছে বিশ্বমানুষের আপনজন।
‘ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা
তোমাতে বিশ্বময়ী, বিশ্ব মায়ের অাঁচল পাতা’
রবীন্দ্রনাথ ভালোবাসতেন পৃথিবী ও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষকে। তার কথায়, আমি এই পৃথিবীকে বড় ভালোবাসি। তার মতে, মানুষের মধ্যে বিশ্বের সব বৈচিত্র্যই আছে বলে মানুষ বড়। প্রত্যেক মানুষ যেন স্বকীয় মর্যাদায় বিকাশ লাভ করতে পারে তার জন্য দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার একান্ত প্রয়োজন মনে করতেন। সন্ত্রাস দমনে রবীন্দ্রনাথ বিবর্তনমূলক আইনের অপরিহার্য আবশ্যকতা লক্ষ্য করেন। রাষ্ট্র ও নাগরিকদের ব্যক্তি স্বাধীনতা উভয়ের দিকে দৃষ্টি দেন। বিভিন্ন জাতি ও রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ববোধের সংহতিকল্পে এবং অশান্তি নামের অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধের পক্ষে অনড় ছিলেন। শিক্ষাই মাতৃভাষার মাতৃদুগ্ধ। তিনি মনে করতেন, চিত্ত বিকাশের সবচেয়ে আপন আয়োজন হওয়া উচিত মাতৃভাষায়। শিক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে মানুষকে প্রাণিত করেছেন। তিনি কৃষি উন্নয়ন, শিক্ষা ও জনসাধারণের স্বাস্থ্যসেবার চিন্তা করেছিলেন। শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় ও শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেছেন। শিক্ষায় আগ্রহ ও আনন্দময় করে তোলার ক্ষেত্রে সঙ্গীতকে যোগ করেছেন। কৃষিতে প্রযুক্তি, পল্লী পুনর্গঠনে উদ্যোগী হয়েছেন। সমবায়ভিত্তিক অর্থনৈতিক সমাজ পুনর্গঠনের কর্মসূচি ভারতবর্ষে প্রথম চালু করেন। গ্রাম বাঁচলে দেশ বাঁচবে_ এই তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন।
রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন, শহর নয়, গ্রামই বাংলাদেশের প্রাণস্বরূপ। দেশকে মুক্ত করতে তিনি গ্রামের নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে জাগাতে চেয়েছেন। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ‘স্বদেশি আন্দোলন’কে সমর্থন দেন। বাঙালি জনগোষ্ঠীকে অসাম্প্রদায়িকতা লোকসংস্কৃতির মূল দর্শন বলে বিশ্বাসী ছিলেন। তার কবিতা-গানে, গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ-নাটকে স্বাধীনতার কথা বলেছেন বহুভাবে। জালিয়ানওয়ালাবাগের বর্বর হত্যাকা-ের প্রতিবাদস্বরূপ তিনি ‘স্যার’ উপাধি ত্যাগ করেন। জমিদারি দায়িত্ব পালন করতে এসে কুষ্টিয়ার শিলাইদহ, নওগাঁর আত্রাইয়ের পতিসর ও সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে বসবাস করেন। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় থেকে স্বাধীনতা সংগ্রাম, ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধে তার অবিনাশী গান-কবিতা আমাদের প্রেরণা জুগিয়েছে।
‘বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হোক, পুণ্য হোক
পুণ্য হোক হে ভগবান’
তিনি গ্রামীণ শিল্প ও বিনোদনচর্চাকে উৎসাহ দিয়েছেন। হাতে-কলমে কৃষি শিক্ষা, আদর্শ গ্রাম তৈরি, ব্রতীবালক গঠন করার স্বপ্ন দেখেছেন। টেগোর অ্যান্ড কোং চালু করে চাষিদের ধান-পাট, ভুসিমাল কিনে বাজারে বিক্রির ব্যবস্থা করেন। কৃষকরা যাতে অধিক ফসল উৎপাদন করতে পারে সেজন্য কৃষি ল্যাবরেটরি স্থাপন করেন। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন, প্রকৃত শিক্ষক প্রকৃতিই। বিশ্বভ্রমণ ও প্রকৃতিপ্রেম থেকে সহজেই অনুভব করেছেন জীবনের সঙ্গে যে শিক্ষার যোগ নেই সে শিক্ষা দেশকে স্বয়ম্ভর করে তুলতে পারবে না।
তিনি প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি ও কুফলের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ইংরেজি শিক্ষাকে।
উপলব্ধি করেছেন পশ্চিমের লোক যে বিদ্যার জোরে বিশ্ব জয় করেছে সেই বিদ্যাকে গালি পারতে থাকলে দুঃখ কমবে না বরং অপবাদ বাড়বে। শিক্ষা নিয়ে নানা প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করেন। তিনি এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতিকল্পে আমাদের বিদ্যানিকেতনকে পূর্ব-পশ্চিমের মিলনমেলায় রূপান্তরের স্বপ্ন দেখেছেন।
‘ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো
একলা রাতের অন্ধকারে আমি চাই পথের আলো’
ভারতবর্ষের মহৎ আদর্শের প্রতি যেমন তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তেমনি আস্থাশীল ছিলেন পাশ্চাত্য সভ্যতার মহৎ বৈশিষ্ট্যাবলির প্রতি। পরমতে শ্রদ্ধাশীল মানুষ তিনি। সমাজ বিশ্লেষক হিসেবে ধর্ম, রাজনীতি, সমাজনীতিকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। সাম্প্রদায়িক অপশক্তির বিরুদ্ধে সদা সোচ্চার ও জাগ্রত ছিলেন। রেনেসাঁসের যুক্তিবাদ, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার সমর্থক ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবৎকালে_ রবীন্দ্রনাথ ‘শিক্ষার হেরফের’ নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাকে স্বীকৃতি দিয়ে বলেছেন, প্রতিচিত্রে আপনার মতের সঙ্গে আমার মতের ঐক্য আছে। মানবিক রচনার জন্য মহাত্মা গান্ধী রবীন্দ্রনাথকে ‘মহাপ্রহরী’ অভিধায় অভিহিত করেছেন। মানবীয় চেষ্টা দ্বারাই যে অস্তিত্বশীল বাস্তবের পরিবর্তন সাধনের মধ্য দিয়ে সুন্দরতম, উন্নততর ও সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত সৃষ্টির বাস্তববাদী, অন্বেষণের মনে তিনি সমগ্রতাকে অনুসন্ধান করেছেন। অনন্ত অসীম চিরন্তনতা স্পর্শ করেছেন_ সামগ্রিক বোধে ক্রিয়াশীল বিশ্বভ্রাতৃত্বের ঐক্যে। তার ধর্ম হচ্ছে মানবধর্ম। আন্তর্জাতিকতা রয়েছে তার চিন্তায়। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার ও সুস্পষ্ট মতামত দিয়েছেন। নৈতিক শক্তি ও সংহতির সংমিশ্রণে রবীন্দ্রনাথ মানুষের অন্তরাত্মাকে জাগ্রত করতে আগ্রহী ছিলেন। মূলত মানুষকে ভেবে নতুনভাবে গড়তে সুদূর স্বপ্নবিলাসী হতে দেখা যায়। মানুষের চরম দুর্ভোগের অভিযাত্রাকে অতিক্রম করে চিরকালের মানুষ হিসেবে উন্নতির চিন্তা করেছেন।
‘সুখে আছে যারা সুখে থাক তারা
দুঃখে আছে যারা সুখী হোক তারা’
রবীন্দ্রনাথ মনুষ্যত্ব ও মানবিকতার উৎকর্ষ সাধনে পরমোৎকর্ষে আবেগ, ঐতিহ্য, ইতিহাস, মিথ, পুরাণের আলোকে স্থাপন করেন আন্তঃমানবিকতা। মানুষের মধ্যে ভেদাভেদের সমস্যার প্রতি সজাগ ছিলেন গভীর মমতায়। প্রকৃত অর্থে তিনি সৌন্দর্যবোধ ও মহামানবদের উপলব্ধিকে সারা জীবনই লালন করেছেন। তিনি মনে করেন, পরম সত্তার শ্রেষ্ঠ রূপ হলো বিশ্বমানবের রূপ। অসহায় ও অবহেলিতদের প্রতি দরদ ও সাহচর্য তার মানবতন্দ্রী নীতির মূল কথা। তিনি মানবাত্মার দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাত্মাকে অবলোকন করেছেন মানব কল্যাণে|
|